সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation – PR) চালুর দাবি জানিয়েছে। তাদের মতে, এই পদ্ধতি ভোটের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটায় এবং বড় দলের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙে। তবে বাংলাদেশের রাজনীতি, ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হয় যে, এই পদ্ধতি আমাদের দেশের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। বরং এটি জাতীয় ঐক্য, স্থিতিশীল সরকার এবং উন্নয়নের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইতিহাস বলে, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের ধারাবাহিকতা খুবই দুর্বল। শত শত বছর ধরে আমরা বিদেশি শাসকদের হাতে শাসিত হয়েছি, কারণ নিজেদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। আজ যদি পিআর পদ্ধতি চালু করা হয়, তাহলে আবারও সেই ঐক্যহীনতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, এবং দেশ আরও বেশি অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে।
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR) কী?
পিআর বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হলো এমন একটি নির্বাচন পদ্ধতি যেখানে কোনও দল যত শতাংশ ভোট পাবে, তারা তত শতাংশ আসন পাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনও দল যদি ৩০ শতাংশ ভোট পায়, তাহলে তারা মোট সংসদ আসনের ৩০ শতাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে ধরা হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত একটি জাতীয় বা বড় নির্বাচনি এলাকা ধরা হয় এবং ভোটাররা একটি নির্দিষ্ট প্রার্থীকে নয় বরং একটি দলকে ভোট দেয়। পরে দলগুলো ভোটের অনুপাতে তাদের তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের সংসদে পাঠায়। এটি ‘পার্টি লিস্ট’ ভিত্তিক নির্বাচন হিসেবে পরিচিত। অনেক সময় ভোটারদের দল নির্ধারণের পাশাপাশি তালিকায় থাকা প্রার্থীদের র্যাংক করতেও বলা হয় (যেমন ওপেন লিস্ট পদ্ধতি)। ইউরোপের কিছু দেশ, যেমন নেদারল্যান্ডস, সুইডেন এবং ইসরায়েল এই পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে।
তবে এসব দেশে দলীয় শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক ঐক্য এবং সাংবিধানিক কাঠামো অনেক বেশি দৃঢ়। বাংলাদেশের মতো রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও দলীয় শৃঙ্খলাহীন দেশে এই পদ্ধতি কার্যকর না হয়ে বরং হিতে বিপরীত হবে।
বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি: এফপিটিপি (FPTP)
বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির নাম First-Past-The-Post বা সংক্ষেপে FPTP। এই পদ্ধতিতে দেশকে ৩০০টি নির্বাচনি আসনে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি আসন থেকে একজন প্রার্থী সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। যে প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পান, তিনিই নির্বাচিত হন, যদিও তা মোট ভোটের ৫০ শতাংশ নাও হতে পারে। এর পাশাপাশি আরও ৫০টি নারী আসন দলীয়ভাবে মনোনয়ন দিয়ে পূরণ করা হয়। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, জনগণ সরাসরি একজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন করে, যার মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যাগুলোর প্রতিফলন সংসদে ঘটে।
FPTP পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আছে, যেমন– কোনও দল কম ভোট পেয়েও বেশি আসন পেতে পারে, কিংবা বিরোধী দলের ভোট একাধিক প্রার্থীর মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়ে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী জয়ী হয়ে যেতে পারেন। তবে এই সীমাবদ্ধতার পরেও, বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শাসনক্ষমতার ধারাবাহিকতা এবং প্রশাসনিক গতি বজায় রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছে।
এলাকা ভিত্তিক ছোট দলের আবির্ভাব ও জাতীয় উন্নয়নে বাধা:
পিআর চালু হলে দেশে বহু ছোট আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠবে যারা শুধুই নিজ নিজ এলাকার স্বার্থ নিয়ে কাজ করবে। এই দলগুলোর চিন্তা-চেতনা হবে সীমিত, জাতীয় উন্নয়ন নিয়ে তাদের আগ্রহ কম থাকবে। তারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করবে শুধু নিজ এলাকার জন্য সুবিধা আদায়ে। এতে বৃহৎ পরিসরে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হবে। সরকারের নীতি গ্রহণ ও বাজেট বরাদ্দে দলগুলো নিজের এলাকা নিয়ে টানাটানি করবে, ফলে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কৌশলে ভারসাম্য থাকবে না। জাতির সামগ্রিক অগ্রগতি হবে দুর্বল, আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থানও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজনৈতিক ঐক্যের পরিবর্তে এই ধরনের আঞ্চলিক দলগুলো জাতিকে বিভক্ত করবে, যা একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমাদের পিছিয়ে দেবে।
বিদেশি হস্তক্ষেপ সহজ হয়ে যাবে:
যখন দেশে ছোট ছোট দল গজিয়ে উঠবে, তখন তাদের সাংগঠনিক শক্তি ও আর্থিক সামর্থ্য স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হবে। এই দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রতিবেশী শত্রুদেশ কিংবা বিদেশি শক্তিগুলো তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারবে খুব সহজেই। যেসব দল রাজনৈতিকভাবে দুর্বল, তারা টিকে থাকতে বিদেশি অর্থ ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে, দেশের ভেতরে বহির্বিশ্বের এজেন্ডা বাস্তবায়ন হতে শুরু করে।
এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা বা প্রভাবশালী রাষ্ট্র গোপনে ছোট দলগুলোকে অর্থ, পরামর্শ কিংবা মিডিয়া কাভারেজ দিতে পারে। এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলবে। কোনও জাতীয় নীতিমালা, অবকাঠামো প্রকল্প কিংবা কূটনৈতিক চুক্তির বিষয়ে তারা এসব ছোট দলের মাধ্যমে দ্বিমত তৈরি করবে, বিলম্ব ঘটাবে, কিংবা পুরোপুরি ব্যর্থ করে দিতে পারবে। অতীতেও দেখা গেছে—বিভিন্ন সময় প্রতিবেশী দেশের স্বার্থে কিছু রাজনীতিবিদ বিবৃতি দিয়েছেন বা সংসদে বাধা দিয়েছেন। পিআর চালু হলে সেই সুযোগ আরও বহুগুণে বাড়বে।
কর্তৃত্ববাদী শাসন এবং উগ্রবাদী শক্তির উত্থান:
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে ছোট ছোট দলগুলো সংসদে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে যাবে, এমনকি মাত্র দুই-তিন শতাংশ ভোট পেলেও তারা গুরুত্বপূর্ণ আসন পেতে পারে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী বা আধা-সামরিক আদর্শের দলগুলো রাজনৈতিক বৈধতা অর্জন করতে পারবে। তারা নিজেদের স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আধিপত্য কায়েম করবে, যেখানে তারা ‘নির্বাচিত প্রতিনিধি’ পরিচয়ে জনগণের ওপর চাপ প্রয়োগ ও দমনমূলক আচরণ শুরু করবে।
এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা, এমনকি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। বাংলা ভাইয়ের শাসনের সময় আমরা দেখেছি কীভাবে একটি দল ধর্মের নামে নিরীহ মানুষের জীবনকে আতঙ্কিত করেছিল। এইরকম দলগুলো যখন সংসদে বৈধতা পাবে, তখন তারা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠবে। ফলে প্রধান দলগুলোও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ভয় পাবে কিংবা চাইলে পারবেও না। এতে দেশে আইনের শাসন ও মানবাধিকার রক্ষার কাজ গভীর সংকটে পড়বে।
জাতীয় স্বার্থে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা:
উন্নয়নশীল দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো—দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রতিরক্ষা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জাতীয় বাজেট, বা জরুরি আইন প্রণয়নের মতো বিষয়গুলোতে সরকারকে অনেক সময় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে হয়। FPTP পদ্ধতিতে যে দল সরকার গঠন করে, তারা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হয় বিধায় তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
কিন্তু পিআর চালু হলে সংসদে একাধিক দল থাকবে যাদের স্বার্থ ও মতাদর্শ ভিন্ন। প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য তাদের সঙ্গে সমঝোতায় যেতে হবে। অনেক সময় কোনও ছোট দল যদি একমত না হয়, তাহলে পুরো সংসদে অচলাবস্থা তৈরি হতে পারে। বড় কোনও অবকাঠামো প্রকল্প, প্রতিরক্ষা চুক্তি বা জরুরি আইন পাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। দেশের জাতীয় স্বার্থ তখন বারবার দলীয় মতানৈক্যের সামনে হোঁচট খাবে। বাংলাদেশের মতো একটি দেশ যেখানে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব মানে শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্যও হুমকি।
জোট সরকারের অস্থিতিশীলতা, ছোট দলের অযাচিত প্রভাব ও বিভাজনমূলক রাজনীতি:
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সংকট হলো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন প্রায় অসম্ভব করে তোলা। ফলে সরকার গঠনের জন্য একাধিক দলের ভঙ্গুর জোট গঠন করতে হয়, যা প্রায়ই অস্থির ও অকার্যকর হয়ে দাঁড়ায়। এই জোট সরকারের নীতিনির্ধারণ ও আইন প্রণয়নে অংশীদার দলগুলোর সম্মতি নিশ্চিত করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মারাত্মকভাবে বিলম্বিত হয় বা সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে পড়ে, যার ফলে প্রশাসনিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং নাগরিকদের মধ্যে সরকারের প্রতি আস্থাহীনতা বৃদ্ধি পায়।
এই অস্থিতিশীলতা আরও তীব্র হয় যখন সরকার গঠনে বড় দলগুলোকে দুই-তিনটি আসনধারী ছোট দলগুলোর উপর নির্ভর করতে হয়। এতে করে নগণ্য নির্বাচনি সমর্থনপ্রাপ্ত দলগুলোও নীতিনির্ধারণে অপ্রতুল শক্তির চেয়ে বহুগুণ বেশি প্রভাব খাটিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ এজেন্ডা চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তারা জাতীয় গুরুত্বের সিদ্ধান্তগুলোকে জিম্মি করে ফেলতে পারে, যার ফলে একধরনের ‘রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেইল’-এর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
জবাবদিহির ঘাটতি ও দায়িত্বহীনতা:
পিআর পদ্ধতিতে সাধারণত দলীয় তালিকা অনুসারে প্রার্থী সংসদে যায়। এতে সরাসরি এলাকার মানুষের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে কোনও এলাকার মানুষের সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য একজন নির্দিষ্ট প্রতিনিধি থাকে না, যাকে জনগণ জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারে। দল যদি কাউকে তালিকায় রাখে, তিনিই সাংসদ হবেন, জনগণ তাকে ভোট দিক বা না দিক। এতে করে জনগণের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গণতন্ত্রের মূল আত্মা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
নির্বাচনি পদ্ধতির জটিলতা ও স্থানীয় চাহিদা উপেক্ষা:
পিআর একটি জটিল নির্বাচনি পদ্ধতি। সাধারণ ভোটারদের জন্য এটি বোঝা কঠিন। ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণায় অনেক সময় লেগে যায়, যা ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি করে। উপরন্তু, যেহেতু এই পদ্ধতিতে স্থানীয় আসনের কোনও গুরুত্ব নেই, তাই স্থানীয় চাহিদা, সমস্যা বা উন্নয়ন পরিকল্পনা অনেক সময় উপেক্ষিত থেকে যায়। এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের ধারণাটি দুর্বল হয়ে পড়ে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
নীতিহীন জোটবদ্ধতা:
সরকার গঠনের প্রয়োজনে অনেক সময় আদর্শগতভাবে বিপরীত দলগুলোও একত্রিত হয়ে জোট করে। এতে রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতির চেয়ে ক্ষমতা অর্জনই মুখ্য হয়ে পড়ে। জনগণের কাছে এটি একটি দ্বিচারিতা বা অস্বচ্ছ রাজনীতির বার্তা দেয়, যার ফলে রাজনীতির প্রতি মানুষের আস্থা কমে যায়। আদর্শহীন এই রাজনীতি ভবিষ্যতে রাজনৈতিক চেতনার সংকট তৈরি করতে পারে।
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি অনেক পশ্চিমা দেশে সফলভাবে প্রয়োগ হলেও, বাংলাদেশের সামাজিক গঠন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এটি কার্যকর হবে না বরং ক্ষতিকর হবে। বাংলাদেশের ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঐক্যহীনতা আমাদের বারবার পরাধীনতা, রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও উন্নয়ন স্থবিরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। পিআর পদ্ধতি চালু করা মানে সেই ঐক্যহীনতাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া। ফলে আমাদের বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা দূর করার চেষ্টা করাই শ্রেয়, কিন্তু তা পিআর পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে নয়। আমাদের প্রয়োজন রাজনৈতিক সংস্কারের, দলীয় গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার, যাতে করে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থায়।
লেখক: ব্যারিস্টার, কোর্টস অব ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস




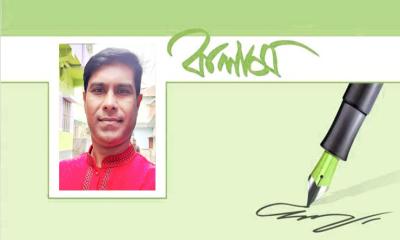

















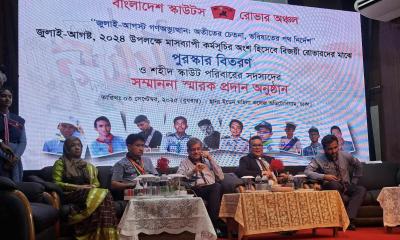





-20250905063727.jpg)



আপনার মতামত লিখুন :